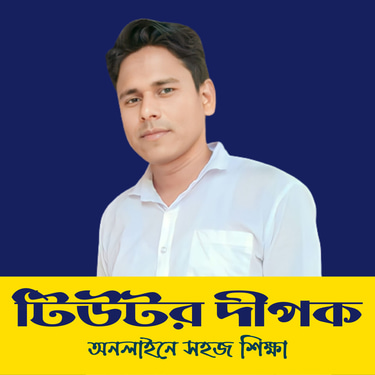চতুর্থ অধ্যায় [সঙ্ঘবদ্ধতার গোড়ার কথা: বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ]
বিভাগ 'ক'
● ১. সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো:
১.১ প্রথম ভারত সচিব নিযুক্ত হন-
(ক) জন মর্লে, (খ) লর্ড স্ট্যানলে, (গ) স্যার চার্লস উড, (ঘ) স্যামুয়েল মন্টেগু।
উত্তরঃ (খ) লর্ড স্ট্যানলে।
১.২ ১৮৫৭-র বিদ্রোহকে 'মুসলমানদের ষড়যন্ত্র' বলেছেন-
জেনারেল আউট্রাম, স্যার হিউরোজ, কর্নেল হোমস, কলিন ক্যাম্পবেল।
উত্তরঃ (ক) জেনারেল আউট্রাম।
১.৩ 1857 IN OUR HISTORY প্রবন্ধটি লিখেছেন-
বীর সাভারকর, রমেশ চন্দ্র মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ সেন, পূরণ চাঁদ জোশি।
উত্তরঃ (ঘ) পূরণ চাঁদ জোশি।
১.৪ বীর কুনওয়ার সিং বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন- কানপুরে, বিহারে, আসামে, বিজনোর-এ।
উত্তরঃ (খ) বিহারে।
১.৫ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের বয়স ২১ থেকে ১৯ করা হয়-
লর্ড ওয়েলেসলি, লর্ড বেন্টিঙ্ক, লর্ড লিটন, লর্ড রিপন-এর আমলে।
উত্তরঃ (গ) লর্ড লিটন-এর আমলে।
১.৬ সর্বভারতীয় জাতীয় সম্মেলনের প্রথম সভাপতি ছিলেন-
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, রামতনু লাহিড়ী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।
উত্তরঃ (গ) রামতনু লাহিড়ী।
১.৭ জমিদার সভা পরবর্তীতে কোন্ সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়-
ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, হিন্দু মেলা, ভারত সভা।
উত্তরঃ (ক) ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি।
১.৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গোরা উপন্যাসটির পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ ঘটে-
১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে, ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে, ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে, ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে।
উত্তরঃ (খ) ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে।
১.৯ স্বদেশ প্রেমের গীতা নামে পরিচিত-
আনন্দমঠ, গোরা, বর্তমান ভারত, দেবী চৌধুরানী।
উত্তরঃ (ক) আনন্দমঠ।
১.১০ ভারত মাতা চিত্রটি কোন দেবীর অনুকরণে আঁকা-
দেবী দুর্গা, দেবী লক্ষ্মী, দেবী কালী, দেবী জগদ্ধাত্রী।
উত্তরঃ (খ) দেবী লক্ষ্মী।
বিভাগ- 'খ'
উপবিভাগ-২.১
● একটি বাক্যে উত্তর দাও।
২.১.১ হিন্দুমেলার প্রচার পত্রিকার নাম কী?
উত্তরঃ হিন্দুমেলার প্রচার পত্রিকার নাম হল জাতীয় পত্রিকা বা ন্যাশনাল পেপার।
২.১.২ বন্দেমাতরম্ সংগীতটি কোন উপন্যাসের অন্তর্গত।
উত্তরঃ বন্দেমাতরম্ সংগীতটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আনন্দমঠ উপন্যাসের অন্তর্গত।
২.১.৩ ইলবার্ট বিল কার আমলে প্রকাশিত হয়?
উত্তরঃ ইলবার্ট বিল প্রকাশিত হয় বড়লাট লর্ড রিপনের আমলে।
২.১.৪ বর্তমান ভারত রচনাটি প্রথম প্রকাশিত হয় কোন পত্রিকায়?
উত্তরঃ বর্তমান ভারত রচনাটি প্রথম প্রকাশিত হয় উদ্বোধন পত্রিকায়।
২.১.৫ ভারতমাতা চিত্রটি কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে আঁকা হয়?
উত্তরঃ ভারতমাতা চিত্রটি ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে আঁকা হয়।
২.১.৬
২.১.৭
২.১.৮
২.১.৯
২.১.১০
২.১.১১
উপবিভাগ-২.২
● ঠিক বা ভুল নির্ণয় কর।
২.২.১ ১৮৫৭-র বিদ্রোহে প্রথম বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয় বহরমপুরে।
উত্তরঃ ঠিক।
২.২.২ ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনের দ্বারা এদেশে কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে।
উত্তরঃ ঠিক।
২.২.৩ হিন্দু মেলা সংগঠনটির প্রথম নাম ছিল জাতীয় মেলা।
উত্তরঃ ঠিক।
২.২.৪ গোরা রচনাটি প্রথম বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
উত্তরঃ ভুল।
২.২.৫
উত্তরঃ ভুল।
উপবিভাগ- ২.৩
● 'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মেলাও।
২.৩.১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - (ক) রাষ্ট্রগুরু
২.৩.২ সুরেন্দ্রনাথ সেন - (খ) জাতীয় পত্রিকা
২.৩.৩ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় - (গ) গোরা
২.৩.৪ নবগোপাল মিত্র - (ঘ) Eighteen Fifty Seven.
উত্তরঃ ১>গ, ২>ঘ, ৩>ক, ৪>খ
উপবিভাগ ২.৪
● প্রদত্ত ভারতবর্ষের রেখা মানচিত্রে নিম্নলিখিত স্থানগুলি চিহ্নিত করো ও নাম লেখো।
২.৪.১ মহাবিদ্রোহের কেন্দ্র দিল্লি।
২.৪.২ ব্যারাকপুর।
২.৪.৩ ঝাঁসি।
২.৪.৪ কানপুর।
২.৪.৫
উপবিভাগ ২.৫
● নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির সঙ্গে সঠিক ব্যাখ্যাটি নির্বাচন করো।
বিভাগ 'গ'
৩. দুটি অথবা তিনটি বাক্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।
৩.১ উনিশ শতকে জাতীয়তাবোধের উন্মেষে ভারতমাতা চিত্রটির কীরূপভূমিকা ছিল?
উত্তরঃ ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলন চলাকালে ভারতমাতা চিত্রটি অঙ্কন করেন চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
ধনদেবীর লক্ষ্মীর অনুকরণে আঁকা ভারতমাতা চিত্রটিতে দেবী শ্বেত বস্ত্র, রুদ্রাক্ষের মালা, বেদ, ও ধানের গোছা ধারণ করেছেন। এইগুলিকে শিক্ষা, দীক্ষা, অন্ন ও বস্ত্রের প্রতীক রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। যা ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বাহক। চিত্রটির দ্বারা বৃটিশ শাসনকালে ভারতীয়দের মধ্যে দেশপ্রেম তথা জাতীয়তা বোধ জাগ্রত হয়েছে।
৩.২ ব্যঙ্গচিত্র কেন আঁকা হয়?
উত্তরঃ ব্যঙ্গচিত্র বা কার্টুন হল এক ধরনের চিত্রকলা।
ব্যঙ্গচিত্র আকার কারণ-
(১) সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ত্রুটিগুলি তুলে ধরতে,
(২) শৈল্পিক ভাবনার মাধ্যমে নানা অসংগতির প্রতিবাদ জানাতে, এছাড়া
(৩) নিছক বিনোদন হেতু ব্যঙ্গচিত্র আঁকা হয়।
৩.৩ সভাসমিতির যুগ কী?
উত্তরঃ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ অর্থাৎ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কালপর্বে ভারতীয়রা সারাদেশে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সভা সমিতি গঠন করে। এই কারণে কেমব্রিজ ইতিহাসকার অনিল শীল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধকে সভা-সমিতির যুগ বলে অভিহিত করেছেন।
বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা, জমিদার সভা, জাতীয় কংগ্রেস প্রভৃতি হল এই যুগের উল্লেখযোগ্য সংগঠন।
৩.৪ আনন্দমঠ উপন্যাস কিভাবে জাতীয়তাবাদী ভাবধারাকে উদ্দীপ্ত করেছিল?
উত্তরঃ সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা আনন্দমঠ উপন্যাস হল একটি কালজয়ী বাংলা উপন্যাস।
ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালে দেশমাতার লুপ্ত স্বাধীনতা ও গৌরব পুনরুদ্ধার করতে ভারত সন্তানদের (সন্তানদল) আত্মশক্তি গঠন ও আত্ম বলিদানের পন্থা নির্দেশ করা হয়েছে আনন্দমঠ উপন্যাসে। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বীজমন্ত্র 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি আনন্দমঠ উপন্যাস থেকেই গৃহীত হয়েছে।
৩.৫ নবগোপাল মিত্র কে ছিলেন?
উত্তরঃ নবগোপাল মিত্র ছিলেন একজন ভারতীয় নাট্যকার, কবি, প্রাবন্ধিক ও দেশপ্রেমিক। ১৮৬৭ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু জাতীয়তাবাদী সংগঠন হিন্দুমেলা-র প্রাণপুরুষ ছিলেন নবগোপাল। ন্যাশনাল প্রেস, ন্যাশনাল পেপার, ন্যাশনাল সোসাইটি, ন্যাশনাল স্কুল, ন্যাশনাল থিয়েটার, ন্যাশনাল স্টোর, ন্যাশনাল জিমন্যাসিয়াম এবং ন্যাশনাল সার্কাস; এই সংগঠনগুলি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি ন্যাশনাল নবগোপাল নামে পরিচিত ছিলেন।
৩.৬ শিক্ষিত সমাজের একটি অংশ কেন মহাবিদ্রোহের বিরোধিতা করেছিলেন?
উত্তরঃ কতিপয় বিশিষ্ট বিদ্যজন ছাড়া প্রায় সমগ্র শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বাঙালি ১৮৫৭ বিদ্রোহে সরকারের পক্ষ অবলম্বন করে বিদ্রোহের বিরোধিতা করেছিলেন। কারণ-
(১) ব্রিটিশ প্রশাসনে চাকরি হারানো ও বিরাগভাজন হওয়ার ভীতি,
(২) ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন মধ্যযুগীয় বর্বরতা প্রত্যাবর্তনের আশঙ্কা,
(৩) ব্রিটিশ সরকারের সংস্কারমূলক কর্মসূচির দ্বারা উন্নত সমাজ গঠনের ইতিবাচক প্রভাব। এই সমস্ত কারণে শিক্ষিত সমাজের একটি অংশ মহাবিদ্রোহের বিরোধিতা করেছিলেন।
৩.৭ এন্ডফিল্ড রাইফেলের ঘটনাটি কী?/মহাবিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ কী?
উত্তরঃ এনফিল্ড রাইফেল হল ব্রিটিশ আমলে সামরিক বাহিনীতে ব্যবহৃত এক ধরনের বন্দুক। বন্দুকে ব্যবহৃত টোটার খোলসটি দাঁতে কেটে বন্দুকে ভরতে হত। শোনা যায়, ব্রিটিশরা হিন্দু ও মুসলিম ভারতীয়দের ধর্মনাশের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে টোটার খোলস বা মোড়কটি গরু ও শূকরের চর্বি দিয়ে তৈরি করত। এতে ভারতীয় সেনারা ক্ষোভে ফেটে পড়ে। (সমাপ্তি বাক্য প্রশ্ন অনুযায়ী লিখতে হবে।)
৩.৮ ১৮৫৭ বিদ্রোহকে জাতীয় বিদ্রোহ বলার যুক্তি কী?
উত্তরঃ ১৮৫৭-র বিদ্রোহকে ডিস্রেলি, ম্যালেসন, আউটড্রাম, কার্ল মার্কস প্রমুখরা জাতীয় বিদ্রোহ বলেছেন অভিহিত করেছেন। কারণ,
(১) ভারতের বিভিন্ন অংশের জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে মেতে উঠেছিল।
(২) বিদ্রোহীরা মুঘল শাসক ২য় বাহাদুর শাহকে জাতীয় সম্রাট ঘোষণা করে ভারতে ব্রিটিশ মুক্ত দেশীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। -এইজন্যই ঐতিহাসিকরা এই বিদ্রোহকে জাতীয় বিদ্রোহ বলেছেন।
৩.৯ হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কী ছিল?
উত্তরঃ নবগোপাল মিত্র কর্তৃক ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু মেলা (পূর্ব নাম জাতীয় মেলা) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল-
(১) ভারতীয়দের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করা। (২) সনাতন হিন্দু সংস্কৃতির বীরগাথা শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে প্রচার করা।
(৩) দেশীয় ভাষা চর্চা ও শিল্পকর্মে উন্নতি সাধন, ইত্যাদি।
৩.১০ জমিদার সভা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কী?
উত্তরঃ ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত জমিদার সভার উদ্দেশ্য ছিল-
(১) বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার জমিদারদের জমিদারিস্বার্থ রক্ষা করা।
(২) ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রকে জমিদারদের পক্ষে নিয়ে আসা।
(৩) জমিদার শ্রেণীর উন্নতিকল্পে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসার ঘটানো, ইত্যাদি।
৩.১১ ইলবার্ট বিল বিতর্ক কী?
উত্তরঃ ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড রিপনের আমলে ইলবার্ট বিল প্রবর্তিত হয়। এই বিলে ভারতীয় বিচারকদেরকে ইউরোপীয়দের বিচারের অধিকার দেওয়া হলে তারা (ইউরোপীয়রা) বিলটির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। অপরদিকে ভারত সভা উক্ত বিলের সমর্থনে একটি প্রতিআন্দোলন গড়ে তোলে। ইলবার্ট বিলকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হওয়া এই বিতর্ক 'ইলবার্ট বিল বিতর্ক' নামে পরিচিত।
বিভাগ 'ঘ'
৪. সাত বা আটটি বাক্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।
৪.১ জাতীয়তাবাদের প্রসারে হিন্দুমেলার ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।
■ জাতীয়তাবাদের প্রসারে হিন্দুমেলার ভূমিকা:
● ভূমিকা: উনিশ শতকের বাংলায় যে সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠেছিল, ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের ১২ই এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হিন্দুমেলা ছিল তার মধ্যে অন্যতম।
সনাতন হিন্দু সংস্কৃতির আদর্শে ভারতীয়দের মধ্যে স্বদেশ ভাবনার প্রসার ঘটাতে নবগোপাল মিত্র হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠা করেন।
● হিন্দু মেলার কার্যকলাপ:
হিন্দু মেলা জাতীয়তাবাদ প্রসারে বিভিন্ন কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছিল। যেমন-
(১) দেশাত্মবোধ জাগরণ:
প্রতিষ্ঠানের অন্যতম সদস্য সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'মিলে সবে ভারত সন্তান" গানটি রচনা করে ভারতীয়দের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করেন।
(২) ধর্মীয় সমন্বয় সাধন:
প্রতিষ্ঠানটির প্রাণপুরুষ নবগোপাল মিত্র জাতীয় পত্রিকা (ন্যাশনাল পেপার)- এর মধ্য দিয়ে হিন্দু-ইসলাম- খ্রিস্টান- পারসিক সকল ধর্মের সমন্বয়ে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রচার করেন।
(৩) অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা:
শিল্পচর্চার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটিয়ে ভারতীয়দের আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করে হিন্দু মেলা।
(৪) স্বতন্ত্রতা রক্ষার পথপ্রদর্শক:
আলোচ্য সংগঠনটি ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রথম প্রদর্শক এর ভূমিকায় পালন করে।
● মন্তব্য: এইভাবে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, সমাজ, স্বাস্থ্য, শিল্প প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটিয়ে ভারতীয়দের একসূত্রে বাঁধতে উদ্যোগী হয়েছিল হিন্দু মেলা।
৪.২ গোরা উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদী ভাবধারা কীভাবে ফুটে উঠেছে?
■ গোরা উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদী ভাবধারার পরিস্ফুটন:
●ভূমিকা: উপনিবেশিক শাসনকালে ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রসারে যে সকল সাহিত্য উপাদান উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গোরা উপন্যাস তার মধ্যে অন্যতম।
● গ্রন্থ পরিচয়:
গোরা রচনাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পঞ্চম তথা দীর্ঘতম উপন্যাস। প্রথমে প্রবাসী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের পর ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয় উপন্যাসটি।
● জাতীয়তাবাদী উন্মেষ:
(১) ভারতের স্বরূপ উদঘাটন:
রবীন্দ্রনাথ তাঁর গোরা উপন্যাসে সত্যনিষ্ঠা, ত্যাগ, বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য ও মিলন, মানবতা, বিশ্বজনীন প্রেম ইত্যাদি চরিত্রের দ্বারা ভারতবর্ষের প্রকৃত রূপের পরিচয় দিয়েছেন।
(২) স্বদেশ প্রেম:
উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র গোরার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশপ্রেমের মহিমা প্রচার করেছেন। গোড়া একাধারে সংস্কৃতিবান হিন্দু ব্রাহ্মণ, অপরদিকে নির্ভেজাল একজন দেশপ্রেমিক।
(৩) সম্প্রীতির আদর্শ প্রচার:
গোরা উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রে রবীন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা প্রদান করেছেন। হিন্দু -মুসলিম- খৃষ্টান -ব্রাহ্মণ সকল ভারতীয়র যিনি দেবতা, তার আদর্শে গোরার চরিত্র গঠন করেছেন রবীন্দ্রনাথ।
(৪) বিশ্বজনীন প্রেম:
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরোধী ছিলেন। গোরা উপন্যাসের মাধ্যমে তিনি বিশ্বজনীন প্রেম ও ভাতৃত্ববোধকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।
● মূল্যায়ন:
আলোচনার শেষে একথা উল্লেখের দাবি রাখে যে, গোরা হলো একটি সর্বাঙ্গীণ জাতীয়তাবাদী উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্ট গোরা চরিত্রটির মধ্য দিয়ে ভারতীয়দের জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে সম্পূর্ণরূপে সচেষ্ট হয়েছেন।
৪.৩ মহাবিদ্রোহের প্রতি শিক্ষিত বাঙালি সম্প্রদায়ের মনোভাব কীরূপ ছিল?
● ভূমিকা:
ভারতের ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংঘটিত প্রথম সর্বাত্মক গণবিদ্রোহ হল ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ। কতিপয় বিশিষ্ট বিদ্বজন ব্যতীত শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বাঙালি সমাজের একটি বড় অংশ সরকারের পক্ষ অবলম্বন করে মহাবিদ্রোহের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।
● বিরোধিতার কারণ:
(১) ব্রিটিশ প্রশাসনে চাকরি হারানো ও বিরাগভাজন হওয়ার ভীতি,
(২) ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন মধ্যযুগীয় বর্বরতা প্রত্যাবর্তনের আশঙ্কা,
(৩) ব্রিটিশ সরকারের সংস্কারমূলক কর্মসূচির দ্বারা উন্নত সমাজ গঠনের ইতিবাচক প্রভাব। -এই সমস্ত কারণে শিক্ষিত সমাজের একটি অংশ মহাবিদ্রোহের বিরোধিতা করেছিলেন।
● বিরোধিতার বিভিন্ন দিক:
(১) সভাসমিতির দ্বারা বিরোধিতা:
ভারতসভা, কলকাতা মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতি সভাসমিতি গুলি বিদ্রোহের কড়া সমালোচনা করেছিল।
(২) পত্র-পত্রিকার দ্বারা বিরোধিতা:
সমকালীন বিভিন্ন সংবাদপত্র যেমন- সংবাদ প্রভাকর, সম্বাদ ভাস্কর, হিন্দু পেট্রিয়ট প্রভৃতি পত্র-পত্রিকাগুলি বিদ্রোহের বিরোধীতা করে সরকারি দমননীতির পক্ষ অবলম্বন করেছিল।
(৩) সরকারের প্রতি সমর্থন প্রকাশ:
বিদ্রোহ চলাকালে কলকাতার জমিদার, মুৎসুদ্দি (হিসাব রক্ষক) ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী একত্রিত হয়ে সংকটময় পরিস্থিতিতে সরকারকে সকল প্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।
(৪) আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকলাপ:
বিদ্রোহ চলাকালে কলকাতা , শ্রীরামপুর, কোন্নগর প্রভৃতি এলাকার জমিদার ও তালুকদাররা ব্রিটিশ রাজের জয়কামনারার্থে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন। কালীঘাটের মন্দিরে মহা পূজার আয়োজন করে রাজভক্তি প্রকাশ করেন ভবানীপুরের জমিদার।
(৫) ব্যতিক্রমী দিক: অধিকাংশ বাঙালি বুদ্ধিজীবী বিদ্রোহের বিরোধিতা করলেও শ্যামসুন্দর সেন তাঁর সমাচার সুধাবর্ষণ পত্রিকায় বিদ্রোহের সমর্থনে মতামত প্রকাশ করেন।
● মন্তব্য: উপনিবেশিক শাসনকালে বিদ্যাসাগরের মতো কিছু ব্যতিক্রমী চরিত্র থাকলেও অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালি মহাবিদ্রোহকে সুনজরে দেখেননি।
৪.৪ ভারত সভা প্রতিষ্ঠা ও বিকাশে সুরেন্দ্রনাথের ভূমিকা আলোচনা করো।
■ ভারত সভা প্রতিষ্ঠা ও বিকাশে সুরেন্দ্রনাথের ভূমিকা:
●ভূমিকা:
উপনিবেশিক ভারতে ভারতীয়দের সংগঠিত করতে ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারার বিকাশ ঘটাতে যে সমস্ত সভাসমিতি গুলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারত সভা ছিল তার মধ্যে অন্যতম।
● প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে:
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের উদ্যোগে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬ শে জুলাই কলকাতার এলবার্ট হল (বর্তমান কফি হাউস)- এ ভারত সভা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। রেভারেন্ট কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসু ছিলেন যথাক্রমে ভারত সভার প্রথম সভাপতি ও সম্পাদক।
● ভারত সভার বিকাশের সুরেন্দ্রনাথ-এর ভূমিকা:
ভারত সভার প্রাণপুরুষ ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারত সভার বিকাশে তিনি বিভিন্ন কার্যকরী ভূমিকা পালন করেন।
(১) ভারতের ঐক্য সাধন:
রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যসাধনের দ্বারা ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তোলেন।
(২) সিভিল সার্ভিস সংক্রান্ত আন্দোলন:
প্রশাসনে আমলা নিয়োগের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের বয়সসীমা ২২ করার দাবিতে সুরেন্দ্রনাথ ভারতীয়দের সংগঠিত করতে সচেষ্ট হন।
(৩) জনমত গঠনে ভূমিকা:
দি বেঙ্গলি পত্রিকা প্রকাশ করে সুরেন্দ্রনাথ সারা ভারতে জনমত গঠন করেন। দেশীয়দের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভারত সভার শাখা প্রতিষ্ঠা করেন।
(৪) অন্যান্য পদক্ষেপ:
সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বাধীন ভারত সভা ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে সর্বভারতীয় জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করে। এর ফলে জাতীয় আন্দোলনে নতুন প্রাণসঞ্চার ঘটে। কৃষক স্বার্থর রক্ষা, অস্ত্র আইন, দেশীয় সংবাদপত্র আইন ও বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে ভারত সভা জাতীয় স্বার্থে বিভিন্ন কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছিল।
● মূল্যায়ন:
ভারত সম্পর্কে ইউরোপীয়দের চিন্তাধারা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের প্রকৃত রূপ উৎঘাটনের পাশাপাশি জাতীয় আন্দোলনের বিকাশে সুরেন্দ্রনাথ ও ভারত সভার ভূমিকা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।
৪.৫ 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা'-কে প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলা হয় কেন ?
● ভূমিকা: উনিশ শতকের ভারতে প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা'।
◆ প্রতিষ্ঠা:
টাকির জমিদার কালিনাথ রায়চৌধুরী, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখের উদ্যোগে ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়।
এই সভায় প্রথম সভাপতিত্ব করেন গৌরীশংকর ভট্টাচার্য (তর্কবাগীশ) এবং সম্পাদক ছিলেন পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন ।
◆ উদ্দেশ্য: এই সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল-
(১) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি।
(২) দেশীয় স্বার্থবিরোধী সরকারি নীতির সমালোচনা করা।
● কার্যকলাপ:
◆ কোম্পানি নিষ্করভূমির ওপর কর আদায় শুরু করলে, জনগণের স্বার্থরক্ষায় এই সভা তার প্রতিবাদ জানায়।
◆ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য প্রসারের জন্য এই সভা প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করে।
◆ বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা আলোচনা ও বিতর্কের মাধ্যমে সরকারি নীতির রাজনৈতিক ভাবে সমালোচনা করত।
● মূল্যায়ন: ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর 'সংবাদ প্রভাকর' -এ মন্তব্য করেছেন যে, 'রাজকীয় বিষয়ের বিবেচনার জন্য অপরাপর যে সভা হইয়াছিল, তন্মধ্যে বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভাকে প্রথম বলিতে হইবেক'। গবেষক যোগেশচন্দ্র বাগল এটিকে 'বাঙালি তথা ভারতবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান' বলে মন্তব্য করেছেন।
এই সভা দীর্ঘদিন স্থায়ী না হলেও ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক সংগঠন 'জমিদার সভা' -র অগ্রদূত ছিল । তাই বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভাকে ভারতের প্রথম জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে চিহ্নিত করা হয় ।